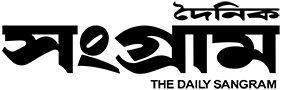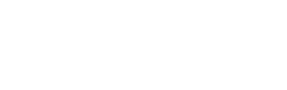ভঙ্গুর অর্থনীতি ও উত্তরণে করণীয়
গত এক যুগের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্নের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। অনেক সংস্থা প্রক্ষেপণ করেছিল যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০২৪ সালের মধ্যে মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুরকে ছাড়িয়ে বিশ্বের ৩০তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠবে।
Printed Edition

এম এ মাসুম
গত এক যুগের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্নের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। অনেক সংস্থা প্রক্ষেপণ করেছিল যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০২৪ সালের মধ্যে মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুরকে ছাড়িয়ে বিশ্বের ৩০তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠবে। সাবেক সরকারের কিছু মন্ত্রী আরো কয়েকধাপ এগিয়ে বাংলাদেশকে কানাডার সঙ্গেও তুলনা করেছিলেন। আগামী ২০২৬, ২০৩৩, ২০৪৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এরকম কত কল্পকাহিনী শুনে কখনো নিজেকে ধনী নাগরিক ভাবতে শুরু করতেন। কিন্তু গত বছরের ০৫ আগস্ট সরকারের পতনের পরপরই দেশের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হতে শুরু হয়েছে।
প্রকৃতপক্ষে গত ১৫ বছরে সুশাসনের অভাব বিশেষ করে রাষ্ট্রের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন দুষ্টচক্রের উত্থান ঘটেছে। বিগত চার-পাঁচ বছরের বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহ ভঙ্গুর এবং নাজুক পরিস্থিতির জন্য কিছুটা দায়ী। যেমন করোনা মহামারি এবং ইউক্রেন যুদ্ধ, বিশ্বের আর দশটা দেশের মতো, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শ্লথ করেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়টি সবাই অনুভব করছে, তার কারণ কিন্তু আসলে দেশজ। বর্তমানে যে অবস্থা তৈরি হয়েছে, তার কারণ অতীতের দিনগুলোয় রাষ্ট্রের সব অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধ ভঙ্গ করা হয়েছে, জবাবদিহিতার সব কাঠামো নষ্ট করা হয়েছে, সব ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করা হয়েছে-এক কথায়, সার্বিক এক অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা বাংলাদেশ অর্থনীতিকে আজকের সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।
ব্যাংক লুটেরাদের স্বর্গরাজ্য
পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের ব্যাংকিং খাত লুটেরাদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। দেশের আর্থিক খাতের অন্যতম অভিশাপ বলে চিহ্নিত এস আলম গ্রুপের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে দেশের বৃহৎ ও অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যাংক হিসেবে খ্যাত ইসলামী ব্যাংসসহ আটটি ব্যাংক দখলে নিয়ে যায়। এসব ব্যাংক থেকে জনগণের আমানতের অর্থ পানির মতো বের করে নিতে থাকে। গণমাধ্যমের তথ্য থেকে জানা যায়, ইসলামী ব্যাংকসহ আট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এস আলম গ্রুপ নামে-বেনামে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বের করে নিয়েছেন ২ লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া আরো ডজনখানেক ব্যাংক থেকে তার ঋণ নেয়ার স¤পৃক্ততা পাওয়া গেছে। এসব ব্যাংকে তদন্ত চলছে। সব মিলিয়ে দেশের ব্যাংকিং খাত থেকে এস আলম গ্রুপের অর্থ বের করে নেয়ার পরিমাণ পৌনে চার লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে পিছিয়ে নেই বেক্সিমকো গ্রুপও। বেক্সিমকো শিল্প পার্কে থাকা ৩২টি কো¤পানির অর্ধেক অর্থাৎ ১৬টিরই কোনো অস্তিত্ব নেই বলে জানিয়েছেন শ্রম উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। অথচ এসব কো¤পানির নামেই ঋণ রয়েছে ১২ হাজার কোটি টাকা। ১৬টি ব্যাংক ও ৭টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে বেক্সিমকো গ্রুপের ৭৮টি প্রতিষ্ঠানের দায়ের পরিমাণ ৫০ হাজার ৯৮ দশমিক ৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টের লকারে তল্লাশি চালিয়ে ব্যাংকটির সাবেক ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার (এস কে) সুর চৌধুরীর রাখা ৫৫ হাজার ইউরো, ১ লাখ ৬৯ হাজার ৩০০ মার্কিন ডলার জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৭০ লাখ টাকার এফডিআর ও প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকা মূল্যের এক কেজি (প্রায় ৮৬ ভরি) সোনার অলংকার জব্দ করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের ব্যাংক খাত থেকে বিভিন্ন লুটেরা মিলেমিশে ১০ লক্ষ কোটি টাকা নানাভাবে লোপাট করে বিদেশে পাচার করেছেন যা দেশে ফিরিয়ে অনা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এভাবেই রাষ্ট্রীয় মদদে দেশের ব্যাংক খাতকে লুন্ঠনের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হয়েছে। বিশেষ করে শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং খাতকে স্থায়ীভাবে নিঃশেষ করার একটি মাস্টার প্ল্যান হাতে নিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার।
ডলার সংকট
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অদক্ষ ও অপরিণামদর্শী নীতির ফলে মুদ্রাবাজারে মার্কিন ডলারের দাম আটকে রেখে স্থানীয় টাকাকে শক্তিশালী দেখানো হয়। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে খাদ্য ও জ্বালানির দাম বেড়ে গিয়ে আমদানি খরচ বেড়ে যায়। এ সময় বাধ্য হয়ে ডলারের দাম কিছুটা বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তাতে দুর্বল হতে শুরু করে টাকা এবং বেড়ে যায় মূল্যস্ফীতি। অন্যদিকে, ডলার বিক্রি করায় বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে অর্ধেক হয়ে যায়। ডলারের বাজার নিয়ে গত সরকারের সময়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত বছরের জানুয়ারি মাসে বৈদেশিক মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল করতে ক্রলিং পেগনীতি অনুসরণের ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ নীতি অনুসরণ করে কোন সফলতা পাওয়া যায় নাই।
সরকার বদলের পর আহসান এইচ মনসুর নতুন গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি বন্ধ করে দেন। পাশাপাশি ডলারের দাম ১২০ টাকা নির্ধারণ করেন এবং তা আড়াই শতাংশ পর্যন্ত কমবেশি করার সিদ্ধান্ত দেন। এতে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসতে শুরু করে ডলারের বাজার। ৩১ ডিসেম্বর থেকে ডলারের দাম আরও বাজারমুখী করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এদিকে প্রবাসী আয়ও বাড়ে। এতে রিজার্ভের পতন থেমেছে, এখন তা বাড়ছে। অনেক উদ্যোগ নেয়ার পরও দেশের অনেক ব্যাংক ডলার সংকট কাটাতে পারছে না।
সর্বস্তরে দুর্নীতির বিস্তার
আওয়ামী লীগের দেড় দশকের শাসনামলে দেশে দুর্নীতির যে বিস্তার ঘটেছিল, তা ছিল নজিরবিহীন। গত ২১ আগস্ট বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে দেয়া যায় যে, দেশের এমন কোনো খাত নেই, যেখানে লাগামহীন দুর্নীতি হয়নি। বলা চলে এসময় অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও অর্থ লোপাটের চাষাবাদ করা হয়েছে। গত দেড় দশকে দেশে বিভিন্ন খাতে ২৮ ধরনের দুর্নীতি করা হয়েছে। ব্যাংক খাত ছিল সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির জন্য উর্বর খাত।
দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে রিপোর্ট বলা হয়, গত ১৬ বছরে শেখ হাসিনা ও তার পরিবার এবং তাদের সরাসরি প্রশ্রয়ে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমলা, এমপি, মন্ত্রী, পুলিশ, বিচারপতিসহ বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিরা শুধু দেশের টাকা বাইরে পাচার করেছেন ২৩৪ বিলিয়ন ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় ৩০ লাখ কোটির টাকারও বেশি। এ পাচারকৃত গত ৫ বছরে দেশের জাতীয় বাজেটের চেয়ে বেশি যা দিয়ে ৭৮টি পদ্মা সেতু করা যেত। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে মোট পাচারের পরিমাণ ৪০ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এ সময়ে প্রতিবছর পাচার হয়েছে ১৬ বিলিয়ন ডলার বা ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। গত ১৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ১৭ লাখ কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে এবং এর ৪০ শতাংশ বা প্রায় ৭ লাখ কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। পদ্মা সেতু, রেল সংযোগ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও কর্ণফুলী টানেলের মতো মেগাপ্রকল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সীমাহীন লুটপাট, অনিয়ম, দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে। আলোচ্য সময়ে সবচেয়ে দুর্নীতি হয়েছে-ব্যাংকিং খাত, বিদ্যুৎ-জ্বালানি, উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে। ২৯টি প্রকল্পের মধ্যে সাতটি বড় প্রকল্প পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতিটিতে অতিরিক্ত ব্যয় ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি। ব্যয়ের সুবিধা বিশ্লেষণ না করেই প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ৭০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে।
মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী
দেশে দুই বছরের বেশি সময় ধরে ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। এর আগে নিত্যপণ্যের বাজারে এ মাত্রার ঊর্ধ্বমুখিতা এত দীর্ঘ সময় বিরাজ করতে দেখা যায়নি। দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধিতে হ্রাস পেয়েছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও প্রকৃত আয়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দীর্ঘদিন ধরে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা এ মূল্যস্ফীতির জন্য দায়ী করা হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ বহিঃস্থ বা দেশের বাইরের উপাদানগুলোকে। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মূল্যস্ফীতি জেঁকে বসেছে মূলত অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলোর কারণেই। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে না আসার পেছনে নীতিনির্ধারকদের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে না পারাকে দায়ী করছেন বিশ্লেষকরা। তারা মনে করছেন, বিগত সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। আবার মূল্যস্ফীতির হার নিয়ে লুকোচুরি করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ৯/১ শতাংশ মূল্যস্ফীতি প্রচার করলেও প্রকৃত মূল্যস্ফীতির হার অনেক বেশি। শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে দেশের প্রকৃত মূল্যস্ফীতির হার ১৫ থেকে ১৭ শতাংশের মধ্যে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি একধরনের অদৃশ্য ঘাতক। সমাজের সচ্ছল ও ধনী মানুষের ওপর এর তেমন প্রভাব না পড়লেও নিম্নআয়ের মানুষের ওপর এর প্রভাব ব্যাপক। যে মানুষেরা কোনোভাবে নাক ভাসিয়ে দারিদ্র্য সীমার ওপর ভেসে থাকে, তারা মূল্যস্ফীতির কারণে যেকোনো সময় দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে যেতে পারে।
সম্প্রতি আইএমএফের প্রেসক্রিপশনে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এনবিআর সূত্র বলছে, ৪৩ ধরনের পণ্য ও সেবায় ভ্যাট বাড়ানোর পাশাপাশি স¤পূরক শুল্ক বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আইএমএফের প্রেসক্রিপশনে ভ্যাট বাড়ানোর উদ্যোগ কার্যকর হলে বিদ্যমান মূল্যস্ফীতিকে আরো উসকে দেবে এবং আয়বৈষম্য আরো বাড়বে।
উচ্চ সুদের হার
মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক ঋণের সুদের হার ও নীতি সুদহার (রেপো রেট) প্রায় দ্বিগুণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সুদহার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের এ প্রেসক্রিপশন দিয়েছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সংস্থাটির এ প্রেসক্রিপশনে মূল্যস্ফীতি না কমে উল্টো ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে এখনো। বেড়েছে মানুষের ভোগান্তি। সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণ নেয়া কমেছে। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বিনিয়োগ। গত অক্টোবরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮ দশমিক ৩০ শতাংশ যা তিন বছরের বেশি সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আইএমএফ যে প্রেসক্রিপশন দিয়েছিল তা বাস্তবায়ন করেও দেশটি কোনো সাফল্য পায়নি। বরং অর্থনীতিতে আরো চাপ বেড়েছে। সুদের হার বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে খুব বেশি কার্যকরী হচ্ছে না। কারণ মুদ্রানীতি, রাজস্ব নীতি এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় একটি সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশে মুদ্রানীতি কেবল সুদের হার বাড়ানোর মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি কমানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু এর সঙ্গে সমন্বিত পদক্ষেপ, যেমন যথাযথ রাজস্ব নীতি ও বাজার নিয়ন্ত্রণের অভাব থাকায় সাফল্য পাওয়া কঠিন হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, সরকার যদি একই সময়ে বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের সমস্যা সমাধানে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ না করে এবং মুদ্রানীতির পাশাপাশি মূল্যসংযোজন কর বা ট্যাক্স-সংক্রান্ত সমন্বয়ের অভাব থাকে, তবে শুধু সুদের হার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এর ফলে ব্যবসায়ীরা অনেক সময় উচ্চ সুদের হারের চাপ অনুভব করলেও বাজারে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা কমাতে কোনো সুফল পাওয়া যায় না।
দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত তরুণ তরুণী বেকার
দেশে প্রতিবছর ২৪ লাখের মতো তরুণ-তরুণী চাকরির বাজারে প্রবেশ করে। বিবিএস-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশে বর্তমানে ৭ কোটি ৩৮ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে রয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৬ লাখ বেকার। আবার অর্ধ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। সমস্যা হলো, এখানে বেকারত্বের যে সংজ্ঞা ও পরিমাপ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের প্রকৃত অবস্থা ফুটে ওঠে না। বিশ্লেষকদের মতে, দেশে প্রকৃত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১ কোটির বেশি। অর্থনীতির প্রতিটি সূচক যখন ধীর গতিতে চলছে, অন্যান্য সূচকের পাশাপাশি শিল্প আমদানি প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য কমেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ স্থবিরতার পাশাপাশি বেসকরারী শ্রমবাজারের বেহাল দশার ফলে বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে সীমাহীন লোপাটের কারণে বেসরকারী ব্যাংকগুলোতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রায় বন্ধ। ফলে উচ্চ শিক্ষিত বেকার সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে।
সরকারের উচিত হবে, তারুণ্যের উচ্ছ্বাস আর উদ্দীপনাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঠিকভাবে কাজে লাগানো। দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায় উঠে আসছে যে আমরা আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পারব। তবে দেশের শ্রমশক্তির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ বলে যে দেশের শ্রমবাজারের বাস্তবতা কিছুটা বিপরীতমুখী। আমাদের দেশের উৎপাদনশীল শ্রমশক্তির মধ্যে নিট তরুণদের (শিক্ষা, কাজ বা প্রশিক্ষণে যুক্ত নেই এমন) সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দেশের ১৫-২৪ বছরের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ শতাংশই নিট জনগোষ্ঠী, যা বৈশ্বিক গড়ের প্রায় দ্বিগুণ এবং এর বড় অংশই নারী (৬২ শতাংশ)। এ পরিসংখ্যান আমাদের একটি রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি করিয়ে দেয়। আমরা তরুণদের জন্য যথেষ্ট কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছি না। কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা তরুণদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য এসএমই ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে নীতিমালার একটি বড় সংস্কার করা উচিত ঋণ বিতরণ, ব্যবস্থাপনা আর কোন খাতে অর্থায়ন করা যাবে তা সম্প্রসারণ করতে। বিদ্যমান নীতিমালা অনুসারে, এসএমই খাতের অর্থায়ন মূলত উৎপাদনমুখী শিল্প খাত আর কৃষি ক্ষেত্রে করা হচ্ছে। কিন্তু অর্থনীতির আকার যখন বৃদ্ধি পায়, তখন এর ক¤েপাজিশনে সেবা (সার্ভিস) খাতের শেয়ারও তখন বৃদ্ধি পায়।
বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্য চ্যালেঞ্জগুলো হলো-প্রবৃদ্ধি অর্জনের নতুন পথ বের করা, রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ, খেলাপি ঋণ কমানো, ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার এবং জিডিপির তুলনায় কর হার বাড়ানো। আরও আছে সময়মতো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং মানবস¤পদ উন্নয়ন। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের রপ্তানি খাতে সংকোচন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। পণ্য রপ্তানি খাত সংকুচিত হলে তা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের স্থিতির ওপর চাপ সৃষ্টি করে। রপ্তানি আয় কমে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রা টাকার বিনিময় হার বা মান কমে যেতে পারে। স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলে সেটা আবার মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিতে পারে। কাজেই রপ্তানি খাতকে চাঙা রাখা আমাদের অর্থনীতির জন্য এই মুহূর্তে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক বাণিজ্য সচল রাখতে হবে। যে কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রম সফল হতে হলে দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। পণ্য পরিবহনকালে চাঁদাবাজি এখনো চলছে আগের মতোই। মার্কেটে মার্কেটে চাঁদাবাজি হচ্ছে। হয়তো চাঁদাবাজের বদল হয়েছে। কিন্তু চাঁদাবাজি বন্ধ হচ্ছে না। সরকারের প্রশাসনের মধ্যে একটি অসৎ, দুর্নীতিবাজ গোষ্ঠী এখনো ঘাপটি মেরেও বসে আছে। ফলে প্রশাসনিক কাজে কাক্সিক্ষত গতি ফিরছে না। তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। ব্যাংক লোটেরা ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন আদালত, ব্যাংক বীমাসহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকল প্রতিষ্ঠানে সুশাসন, ন্যায়বিচার, ও দক্ষতা নিশ্চিত করা সম্ভব হলেই কেবলমাত্র দেশের টেকসই অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।
লেখক: ব্যাংকার ও অর্থনীতি বিশ্লেষক।