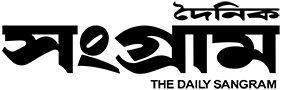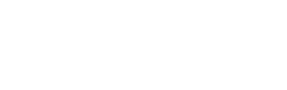সংস্কৃতির অনুসন্ধানে
বাঙালিকে শংকর বলা হলে এ কথার অর্থ দাড়ায় বাঙালি জাতির অস্তিত্ব আগের থেকেই এই অঞ্চলে ছিল, তার সাথে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর লোক মিলেমিশে বাঙালি (সংকর) হয়েছে। কিন্তু না, এ অঞ্চলে বাঙালি নামে কোনো স্বতন্ত্র্য জাতি কখনোই ছিল না।
Printed Edition

ড. মোজাফফর হোসেন
বাঙালিকে শংকর বলা হলে এ কথার অর্থ দাড়ায় বাঙালি জাতির অস্তিত্ব আগের থেকেই এই অঞ্চলে ছিল, তার সাথে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর লোক মিলেমিশে বাঙালি (সংকর) হয়েছে। কিন্তু না, এ অঞ্চলে বাঙালি নামে কোনো স্বতন্ত্র্য জাতি কখনোই ছিল না। বরং সংকর জনগোষ্ঠীই পরবর্তীতে বাঙালি নাম ধারণ করেছে। এই সংকর মানুষগুলো ঠিক কোন সময় থেকে বাঙালি নাম ধারণ করলো বা বাঙালি হিসাবে পরিচিতি পেতে থাকল তা নিয়ে দু এক কথা বলা যেতে পারে। তার আগে দেখা যাক এ অঞ্চলের প্রাচীন জনবসতির বাসিন্দা ছিল কারা। রমেশ চন্দ্র মজুমদার রচিত ‘বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)’ গ্রন্থে প্রাচীন জনপদ বলতে তিনি বঙ্গ, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র রাঢ়া গৌড়ের নাম করেছেন। এসব জনপদে যেসব মানুষ বসবাস করতো তাদের জাতি পরিচয় তিনি উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাতে বাঙালি জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না। রমেশ চন্দ্র উল্লেখ করেন-
‘বাংলাদেশেও আদিম মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কারণ এখানেও প্রধানত পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশের মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে পলিমাটিতে গঠিত হইয়াছিল। প্রস্তর ও তাম্র যুগে সম্ভবত বাংলার পার্ব্বত্য সীমান্ত প্রদেশেই প্রথমে মানুষের বসবাস ছিল। ক্রমে তাহারা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।
বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যগণ যখন পঞ্চনদে বসতি স্থাপন করেন তখন ও তাহার বহুদিন পরেও বাংলা দেশের সহিত তাঁহাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। বৈদিক সূত্রে বাংলার কোনোও উল্লেখ নাই। ঐ তয়ের ব্রাহ্মণে অনার্য্য ও দস্যু বলিয়া যে সমুদয় জাতির উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে পুণ্ড্রেরও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। (বাঙালির নাম নাই)। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গদেশের লোকের নিন্দাসূচক উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রেও পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বর্হিভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং এই দুই দেশে স্বল্পকালের জন্য বাস করিলেও প্রায়শ্চিত্য করিতে হইবে এইরূপ বিধান আছে। এই সমস্ত উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে, বাংলার আদিম অধিবাসীগণ আর্য্যজাতির বংশদ্ভূত নহেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় অন্ত্যজ জাতি দেখা যায় ইহারাই বাংলার আদিম অধিবাসীগণের বংশধর।’
রমেশ চন্দ্র মজুমদারের এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, আদিতে বঙ্গে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব ছিল না। তিনি বলেন অনেক পরে বাঙালি জাতির উদয় হয়েছে এবং আর্যদের সংস্পর্শে এসে। নিচের বক্তব্য পড়লেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হতে পারে। তবুও আমরা বলতে পারি তুর্কি মুসলমানদের আগমনের আগে বঙ্গে বসবাসকারী কেউই নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে সাচ্ছন্দবোধ করতো না। না করার কারণ হলো, এখন যেসব আর্যগোষ্ঠীর লোকজন নিজেদেরকে বাঙালি দাবি করে আধিপত্য বিস্তার করতে চান, তারাই বাঙালি হয়ে ওঠা নিষাদ, দ্রাবির, আলপাইনদেরকে তখন ম্লেচ্চ, দস্যু, অচ্ছুত বলে অপমান করতেন। সেসময়গুলোতে আর্যদের সামনে আত্মসম্মান হারানোর ভয়ে কেউই বাঙালি বলে নিজের পরিচয় দিতে চাইতেন না।
২.
এবার দেখি বাঙালি হয়ে ওঠা সম্পর্কে রমেশ চন্দ্র মজুমদার কী বলেন-
‘নিষাদ জাতির পরে দ্রাবির ভাষাভাষী ও আলপাইন শ্রেণিভূক্ত এক জাতি বাংলাদেশে বাস ও বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি করে। পরবর্তী কালে তাহারা নবাগত আর্য্যগণের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে তাহাদের পৃথক সত্তা ও সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনার ফলে এই বাঙ্গালী জাতির সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায়। বর্তমান কালে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের কয়েকটি বিশিষ্ট অঙ্গ যেমন- কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ, বৈদিক হোম ও যাগযজ্ঞের বিরোধী পূজাপ্রণালী এবং শিব, শক্তি ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর আরাধনা এবং পুরাণবর্ণিত অনেক কথা ও কাহিনী তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। লৌকিক ব্রত, আচার, অনুষ্ঠান, বিবাহ প্রক্রিয়ায় হলুদ, সিন্দুর প্রভৃতির ব্যবহার, নৌকা নির্ম্মাণ ও অন্যান্য অনেক গ্রাম্য শিল্প, ধুতি শাড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট পরিচ্ছদ প্রভৃতিও এই যুগের সভ্যতার অঙ্গ বলিয়াই মনে হয়। মোটের উপর আর্য্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বেই যে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল এই সিদ্ধান্ত যুক্তযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।’
রমেশ চন্দ্র মজুমদারের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, নিষাদ, দ্রাবির ও আলপাইনদের সংস্কৃতি আর্যদের সংস্কৃতির প্রভাবে হারিয়ে যায় এবং পরিবর্তিত আর্য সংস্কৃতি নিয়েই বাঙালি নাম ধারণ করে। রমেশের এই বক্তব্যই এখন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বত্র। অর্থাৎ বাঙালি মানেই আর্য সংস্কৃতির ধারক-বাহক। আরো পরিষ্কার করে বললে বোঝা যাবে যে, আর্য জনগোষ্ঠীর লোকই বাঙালি; মুসলমানরা বাঙালি নয়। এই বক্তব্যের আরেকটা মানে দ্বারায়, সেটা হলো, মুসলমান যদি বাঙালি হতে চায় তবে নিষাদ, দ্রাবির, চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম, আলপাইনদের মতো নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে।
৩.
প্রাচীনকালে বঙ্গ কিংবা বঙ্গালে যে বাঙালির বসবাস ছিল না, তা রিজেলের বক্তব্য থেকেও জানা যায়। স্যার হার্বাট রিজল কর্তৃক রচিত ‘দি পিপল অব ইন্ডিয়া’(১৯০৮) গ্রন্থে দৈহিক বৈশিষ্টের বিচেনায় উপমহাদেশের মানুষকে সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- তুর্কীয়-ইরান, ভারতীয় আর্য, আর্য-দ্রাবিড়, শক-দ্রাবিড়, দ্রাবিড়, মোঙ্গল-দ্রাবিড়, এবং মোঙ্গলীয়। এই সাত ভাগের তিন ভাগ অবিমিশ্র এবং চার ভাগ মিশ্র। এখানেও বাঙালি নামের অস্তিত্ব নাই। কাজেই আদি বাঙালির হদিস মিলে না।
বঙ্গ নামের ব্যাপারে বেশ কিছু গবেষণা আছে। এর মধ্যে রয়েছে ভারতের মহিলা নৃতাত্ত্বিক ইরাবতী কার্ভ কর্তৃক গবেষণা। তার মতে বঙ্গ নামটা আর্যভাষা পরিবারের নয়। নামটা এসেছে চীনা ভাষাপরিবারের কোনো এক ভাষা থেকে। চীনারা সাধারণত নদীর নামের সাথে ‘য়ং’ ধ্বনি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ নদীকে য়ং বলা হয়। যেমন- হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং, সাংপো, দিস্তাং প্রভৃতি। সম্ভবত য়ং থেকে ধ্বনি বিপর্যয়ে বং হয়েছে। আর বং তীরবর্তী লোকেরাই বাঙালি। (ইরাবতী কার্ভ- ‘ইন্ডিয়া এ্যজ এ কালচারাল রিজন’) ইরাবতীর এই গবেষণাও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়।
মুসলিম শাসনামলে ফারসি ভাষার বইপুস্তকে বঙ্গ নামে একটি বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের বর্ণনা পাওয়া যায়। ফারসি ভাষায় এই বিস্তৃর্ণ অঞ্চলকে বলা হতো মুলুক-ই বাঙালাহ। মুসলিম শাসনের আগে দুনিয়াজুড়ে বঙ্গ বা বঙ্গাল নামের পরিচিতি এত ব্যাপক অর্থে ছিল না যা সুলতানি আমলে ছিল। মুলুক-ই বাঙালাহ, সুবে বাঙালাহ নামেও বঙ্গের পরিচিতি ছিল।
বাঙালি শব্দটির উচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুলতানদের সময়ে। বলা হয় বাঙালি জাতিসত্তার উদ্ভব হয়েছে বাংলা ভাষার কারণে। তবে বাংলা ভাষা প্রসিদ্ধ হয়েছে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায়। বৌদ্ধ বা হিন্দু রাজারা এর কৃতিত্বের দাবি করতে পারে না। তুর্কি মুসলমানদের আগমনের আগে বাংলা ভাষায় কোনো পুঁথি লেখা হয়নি। এমন কী বাংলা ভাষায় রামায়ণ মহাভারত তো নয়ই, যে কোনো সাধারণ গ্রন্থ রচনার ব্যাপারেও ছিল নিষেধাজ্ঞা; অমান্য করলে ছিল শাস্তির বিধান। বঙ্গে বসবাসের জন্যও করতে হতো প্রায়শ্চিত্য। এমন অপমান অপদস্ত থেকে বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষী মানুষকে টেনে বের করে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে মুসলমান সুলতানরা। যে বাংলা ভাষা পড়ে আমরা বুঝতে পারি তার উদ্ভবও ঘটেছে তুর্কি মুসলমানদের হাত ধরে। এর আগে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হিসাবে চর্যাপদকে দাবি করা হলেও এর ভাষা পড়ে বুঝা মুশকিল। চর্যাপদ লেখকরা বাঙালি ছিলেন না, তারা ছিলেন বৌদ্ধ। চর্যাপদে যে সংস্কৃতির বিবরণ আছে সেটাও বৌদ্ধদের; বাঙালির নয়। এসব আলোচনা থেকে বলা যায় মর্যাদাবান বাঙালির উৎপত্তি ঘটেছিল সুলতানি আমলে এবং মানবতা ও মানবাধিকারে শ্রেষ্ঠ বাঙালি ছিল মুসলমানরা।
৪.
এ কথা আমরা এখন বলতে পারি যে, প্রসিদ্ধ বাঙালি বলতে যা বুঝি তার পরিচর্যা হয়েছে মুসলমানদের হাতে। মানবতা ও মানবাধিকার বলতে যা বোঝা যায় সে সবেরও বন্দোবস্ত করেছিল মুসলমানরা। মানুষে মানুষে জাত-পাত, উঁচু-নিচুরও অবসান ঘটেছে মুসলমানদের হাত ধরে। তুর্কি মুসলমানরা যে পরিমান ধর্ম প্রচার করেছে তারচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা করেছে মানবাধিকার ও মানবতা। ফলে বাংলার সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সংস্কার হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের। নির্ভয়ে ধর্মের বাণী সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার করতে থাকে মুসলমান হিন্দুসহ সব ধর্মের লেখকরা। ফলে যাদেরকে ম্লেচ্ছ, দস্যু, অচ্ছুত বলা হয়েছিল তারা হয়ে ওঠতে থাকল অন্য সকলেরই মতো সাধারণ মানুষ। বাংলার সংস্কৃতি হয়ে উঠল পরস্পর বিশ্বাসের, মর্যাদার আর মানব কল্যাণের। এর আগে বঙ্গের মানুষ সামাজিক মর্যাদা, মানবিক মূল্যবোধ, ন্যায়বিচার ও আত্মমর্যাদার মতো জনহিতৈশী টার্মগুলোর সাথে পরিচিত ছিল না। মানুষ ছোট ছোট কর্মে নিযুক্ত ও পেশার সাথে যুক্ত থেকেও যে যার মার্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে তার সবক তারা এই প্রথম গ্রহণ করল মুসলমানদের কাছ থেকে। শুধু বঙ্গবাসীরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতিই বদলে দিয়েছিল মুসলমানরা। মুসলমানরা দুনিয়ার সামনে যে অর্থনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা দিয়েছিল তা এখনও পৃথিবীর একমাত্র এবং অদ্বিতীয়। বিনা ইন্টারেস্টে, বিনা শর্তে যে মানুষকে অর্থ-কড়ি দেওয়া যায় তা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছে মুসলমানরা। যাকাত, দান, সাদাকা, কর্জে হাসানা, অসিয়তের মতো শর্তহীন নিঃস্বার্র্থভাবে যে অর্থ-কড়ি একেবারে বিনা লাভে মানুষকে দিয়ে দেওয়া যায় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন মুসলমানরা। অথচ তথাকথিত আধুনিক অর্থ ব্যবস্থায় শর্তহীন নিঃস্বাার্থ লেনেদেনের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি বরং ব্যাংকব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়ে এক অসম অর্থব্যবস্থার সংস্কৃতি চালু রাখা হয়েছে, যাতে দরিদ্র মানুষ আরও বেশি দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের যে বিধিবিধান মুসলমানদের রয়েছে তার সমকক্ষ সংস্কৃতি আজও কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি। অর্থনীতির যে বই বাংলার বিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয়, তাতে বলা আছে, বিনা লাভে অর্থ-কড়ি হাতছাড়া করলে নিঃস্ব হতে হয়। আর মুসলমানদের অর্থনীতির বই শেখায় যাকাত দাও, দান-সদাকা করো, কর্জে হাসানা দাও তোমার সম্পদ পবিত্র হবে ও বৃদ্ধি পাবে। মুসলমানদের অর্থব্যবস্থার সাথে আধুনিক অর্থনীতির এত বৈপরিত্য হলো কেনো? তার খোঁজ করা এবং এর সামাধান বের করার কাজ মুসলমানদেরকেই করতে হবে। মুসলমানদের অর্থব্যবস্থা সব শ্রেণির মানুষের প্রয়োজন বোঝে। কাজেই দ্রুত এ অর্থব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা জরুরি।
শুধু অর্থব্যবস্থা নয়, জীবন যাপনে কল্যাণকর সংস্কৃতির অনুসন্ধান করতে গেলে, মধ্যযুগের বাংলাতে যে উন্নত সংস্কৃতি খোঁজ মিলে, সে সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছিল মুসলমানদের অবদানে। দুঃখের বিষয়, সেই বাংলায় মুসলমানরাই আজ ক্ষতিগ্রস্ত বেশি। কী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তার একটা উদাহরণ দেই। যেমন- যে মুসলমান; দান-সাদাকা করেন, কর্জে হাসানাও দেন এবং যাকাতও পরিশোধ করেন। এই মুসলমান কোনোভাবেই গভর্মেন্ট কর্তৃক ট্যাক্স মৌকুফের সুবিধা পাবেন না। অর্থাৎ এই মুসলমানকে ট্যাক্সও পরিশোধ করতে হবে আবার যাকাতও দিতে হবে। এতে একজন মুসলিম আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কেনো সেটা হবে? তা নিয়ে এখনো কেউ কথা বলেনি। প্রতিবাদ করেনি। সময় এসেছে এ কথা বলার যে, যারা যাকাত আদায় করবে, তাদেরকে যেন ট্যাক্স দিতে না হয়; সে ব্যবস্থা বা আইন রাষ্ট্রে থাকতে হবে। এটা হলে যাকাত আদায়ে মানুষ আগ্রহী হবে এবং মুসলমানদের পক্ষে একটি ফরজ কাজ সম্পন্ন করা সহজ হবে। শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে যাকাতও দিতে হয় আবার ট্যাক্সও দিতে হয়, বিধায় মুসলমান ধনীরা যাকাত আদায় করতে অনিচ্ছা পোষণ করেন এবং আখেরে জবাবদিহির আওতায় আসেন। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্র সেকুলার হওয়ার কারণে মুসলমান তো বটেই সাধারণ গরিব মিসকিন সহায় সম্বলহীন মানুষও যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এখান থেকে পরিত্রাণ দরকার।
জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে একটা নিরপেক্ষ রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তো অবশ্যই তৈরি হয়েছে। এখন দরকার মুসলমানদের আশা-প্রত্যাশার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া। তবে কিছু রাজনৈতিক দল, তারা চায় না দেশে মুসলমানদের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হোক। তারা চায় মানবতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। অসুবিধা নাই। এসব রাজনৈতিক দলের চাওয়ার সাথে মুসলমানদের চাওয়ার কোনো বিরোধ নাই। সত্যিকারের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা পেলে পক্ষান্তরে মুসলমানদের সংস্কৃতিই প্রতিষ্ঠা পাবে। কিন্তু এই দলগুলো শেষ পর্যন্তু মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যে পারে না তা অতীতে দেখা গেছে। এখন দরকার মানবাধিকার প্রশ্নে মুসলমানদের সংস্কৃতি সম্পূরক না পরিপূরক তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মতবিনিময় করা। মানবাধিকারে উৎস নিয়ে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ করা। এই বিশ্লেষণের তত্ত্ব দিয়েই জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে নিয়ে আসা যেতে পারে। নতুন বাংলাদেশের মানুষ মানবাধিকার সমর্থিত সেই সংস্কৃতির প্রত্যাশায় দিন গুণছে ॥
লেখক : প্রাবন্ধিক, শিক্ষক ও গবেষক