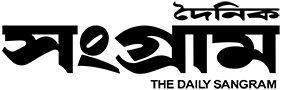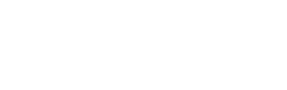কলাম
শুধু সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি দিয়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়
সমস্যার স্বরূপ এবং কেনো এগুলো সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে চায় না। তারা সমস্যার ত্বরিত সমাধান প্রত্যাশা করে। কিন্তু বিগত সাড়ে ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে সৃষ্ট জটিল সব সমস্যা যে রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয় তা কেউ বুঝতে চাইছে না।
Printed Edition
॥ এম এ খালেক ॥
বাংলাদেশ ব্যাংক গত ১০ ফেব্রুয়ারি চলতি অর্থবছরের (২০২৪-২০২৫) জন্য নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে। এটি হচ্ছে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় এবং বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম মুদ্রানীতি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার নানাবিধ আর্থিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা এবং সঙ্কট নিয়ে দেশ পরিচালানা করছেন। এসব সমস্যার প্রায় সবই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। যদিও সমস্যাগুলোর দায়ভার বর্তমান সরকারের উপরই বর্তাচ্ছে। সমস্যার স্বরূপ এবং কেনো এগুলো সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে চায় না। তারা সমস্যার ত্বরিত সমাধান প্রত্যাশা করে। কিন্তু বিগত সাড়ে ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে সৃষ্ট জটিল সব সমস্যা যে রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয় তা কেউ বুঝতে চাইছে না।
আগে থেকেই অর্থনীতিবিদ ও সংশ্লিষ্টদের মাঝে নতুন মুদ্রানীতি কেমন হবে তা নিয়ে এক ধরনের আলোচনা চলছিল। এটা মোটামুটি নিশ্চিত হবে যে, নতুন মুদ্রানীতি সংকোচনমূলক হবে। তবে কতটা সংকোচনমূলক হবে তা ছিল অনুমানের বাইরে। চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ঘোষিত মুদ্রানীতিকে নিশ্চিতভাবেই সংকোচনমূলক বলা যায়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সামনে মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছিল উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং ক্রমহ্রাসমান বিনিয়োগ ধারার মধ্যে যৌক্তিক সমন্বয় সাধন করা। যদি উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বল্প মেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাহলে বিনিয়োগ বিঘিœত হবে, যা দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক স্বল্প সময়ের মধ্যে উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে কমিয়ে আনার উপরই জোর দিয়েছে। ফলে দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক ধরনের স্থবিরতা নেমে আসার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমনিতেই বর্তমানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্থবিরতা বিরাজ করছে। গত জানুয়ারি মাসে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭ দশমিক ২৮ শতাংশ। এটা বিগত ১১ বছরের মধ্যে সর্বনি¤œ ঋণ প্রবৃদ্ধি। একই সময়ে শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল,ক্যাপিটাল মেশিনারিজ এবং মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি ব্যাপক হারে কমেছে। অর্থাৎ ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি এখন অনেকটাই মন্থর হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ আহরণের হারও কমেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ আহরণের পরিমাণ কমেছে ৭১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ১০ কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছিল ৩৬ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি রেট আগের মতো ১০ শতাংশে স্থির রেখেছে। তার অর্থ হচ্ছে আগামীতেও ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমছে না। এমতাবস্থায় অবস্থায় ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ হ্রাস পেতে পারে।
অর্থনীতি সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, শুধু সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি দিয়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। বরং এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা কমে যাবে। যা সার্বিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রমের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। প্রোডাক্টিভ সেক্টরে উৎপাদন কমে গেলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসবে। এটা দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে বিঘিœত করবে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। কারণ উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে তা উচ্চ মূল্যস্ফীতির অভিঘাত মোকাবেলায় ভোক্তাদের সক্ষম করে গড়ে তুলতে পারে। তাই এমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত নয় যার কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট হয়।
অর্থনীতিবিদদের অনেকেই মনে করছেন, বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বর্তমানে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি প্রবণতা বিরাজ করছে তার পেছনে বিগত সরকারের গৃহীত উদ্দেশ্যমূলক ভুলনীতি অনেকাংশে দায়ী। ইউক্রেন যুদ্ধে শুরু হবার পর বিশ^ব্যাপী মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিক গতিতে বাড়তে থাকে। সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। এটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বিগত ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব আমেরিকা (ফেড) সেই সময় পলিসি রেট (সিডিউল ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের সময় যে সুদ প্রদান করে) বারবার বৃদ্ধি করে। এতে ব্যাংক ঋণের সুদের হারও (ব্যাংকগুলো সাধারণ ঋণ গ্রহীতা এবং উদ্যোক্তাদের ঋণ দানের সময় যে সুদ চার্জ করে) আনুপাতিকভাবে বাড়তে থাকে। এতে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ আগের তুলনায় বেশি ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। সাধারণ ঋণ গ্রহীতা ও উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে বাজারে অর্থ সরবরাহ কমে যায়। এটা উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অবদান রাখে। পলিসি রেট বাড়ানোর মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের এ ধারণাটি অত্যন্ত সাধারণ একটি ব্যবস্থা। তবে পলিসি রেট বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ সমস্যা দেখা দেয় তাহলো, এতে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগে স্থবিরতা নেমে আসতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ মন্থর হয়ে পড়ার আশঙ্কাকে বিবেচনায় নিয়েই সাময়িকভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পলিসি রেট বারবার বৃদ্ধি করে। এতে তারা বেশ সফলতাও অর্জন করে। কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি ৩ দশমিক ২শতাংশে নেমে এসেছে। এখন দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক পলিসি রেট বাড়ানোর চিন্তা-ভাবনা করছে। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিশে^র অন্তত ৭৭টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পলিসি রেট বাড়াতে থাকে, যার মধ্যে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অধিকাংশ দেশই এ নীতি অনুসরণ করে উচ্চ মূল্যস্ফীতি যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি শ্রীলঙ্কার মতো সমস্যাগ্রস্থ একটি দেশও তাদের অর্থনীতিতে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতি ৭৭ শতাংশ থেকে মাইনাস টু পয়েন্টে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার এখনো সাড়ে ৯ শতাংশের উপরে রয়েছে।
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি প্রবণতা স্বাভাবিক হয়ে না আসার পেছনে যে কারণটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাহলো, বাংলাদেশ ব্যাংক বারবার পলিসি রেট বাড়ালেও কিছুদিন আগ পর্যন্তও ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার ৯ শতাংশে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। সরকার সমর্থক উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে সুবিধা দেবার মানসেই বাংলাদেশ ব্যাংক এ কাজটি করেছিল বলে অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন। ব্যাংক ঋণের সুদের হার বিদ্যমান মূল্যস্ফীতির চেয়েও কম ছিল। ব্যাংকগুলো এ অবস্থায় ঋণ সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু সরকার সমর্থক বিশেষ গোষ্ঠী তাদের প্রভাব খাটিয়ে ব্যাংক থেকে প্রচুর পরিমাণ ঋণ বের করে নেয়। আগের এক মুদ্রানীতিতে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। বাস্তবে অর্জিত হয়েছিল ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ। একই সময়ে শিল্পে ব্যবহার্য ক্যাপিটাল মেশিনারিজ, কাঁচমাল ও মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি কমেছিল ব্যাপকভাবে। এ লক্ষ্যাতিরিক্ত ঋণ দেয়া হলো ব্যক্তি খাতে তা কোথায় গেল? এক শ্রেণির প্রভাবশালী ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সেই অর্থ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছেন। এমনকি বিদেশে পাচার করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। কোন্ প্রেক্ষিতে সে সময় ব্যাংক ঋণের সুদের সর্বোচ্চ হার ৯ শতাংশে নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল তা তদন্ত করে দেখা হলেই প্রকৃত ঘটনা এবং উদ্দেশ্য বেরিয়ে আসতে পারে। গত কিছুদিন ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি রেট বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যাংক ঋণের সুদের হার নির্ধারণের ইস্যুটি বাজারের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি রেট ১০ শতাংশ এবং ব্যাংক ঋণের সুদের ১৫/১৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু পদক্ষেপটি বড় বিলম্বে নেয়া হয়েছে। যে কারণে এর সুফল পেতে আরো তিন/চার মাস সময় প্রয়োজন হবে।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দেশের অর্থনীতির সার্বিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখানো হয়েছে, বর্ণিত অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি নানা ধরনের জটিলতার মুখোমুখি হয়েছে। সার্বিকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৫ দশমিক ২২ শতাংশ। এর মধ্যে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৩০ শতাংশ, শিল্প খাতে ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ এবং সেবা খাতে ৫ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। খাতগুলোর মধ্যে সেবাখাত তুলনামূলকভাবে ভালো করেছে। একই সময়ে জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ৩৩ লাখ ৪৬ হাজার ১৭ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ দেশের অর্থনীতি নানা কারণেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে কমে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ বিশ^ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (আইএমএফ) বলছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের কিছু বেশি হতে পারে। উল্লেখ্য, বিগত সরকার আমলে অর্থনীতির ইতিবাচক সূচকগুলো উচ্চ মাত্রায় প্রদর্শন করা হতো। যেমন রপ্তানি আয়, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বেশি করে দেখানো হতো। অন্যদিকে আমদানি ব্যয়, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদি পরিসংখ্যান কমিয়ে দেখানো হতো। উদাহরণ হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। বিগত সরকার বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ এক পর্যায়ে ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবার গল্প শুনাতেন। বলা হতো, রিজার্ভের এ পরিমাণ সার্ক দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। একমাত্র ভারতই রিজার্ভ সংরক্ষণের দিক থেকে বাংলাদেশের উপরে আছে। কিন্তু ভারতের মোট রিজার্ভের পরিমাণ কত তা উল্লেখ করা হতো না। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের যে পরিমাণ প্রদর্শন করতো তার মধ্যে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে স্থানান্তরকৃত ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারকে অন্তর্ভ্ক্তু করে দেখানো হতো। এটা এক ধরনের প্রতারণার শামিল। কারণ যে অর্থ আমার কাছে সঞ্চিত নেই এবং চাওয়া মাত্র ব্যবহার করা যায় না তা কখনোই রিজার্ভ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। আইএমএফ বাংলাদেশকে ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের সময় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ হিসাবায়নে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণের শর্ত প্রদান করলে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন নিট রিজার্ভ হিসাব প্রকাশ করছে।
মুদ্রানীতি ঘোষণাকালে বলা হয়েছে, আগামী ৩/৪ মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতির হার ৭/৮শতাংশে নেমে আসবে। কিন্তু কিভাবে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে? শুধু ব্যাংক ঋণের সুদের হার বাড়ালেই উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে এটা বিশ^াস করা যায় না। উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারি।
আগেই বলা হয়েছে, ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছে। চলতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার জিডিপির ২৭ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে। এ লক্ষ্যমাত্রা কোনোভাবেই অর্জিত হবার সম্ভাবনা নেই। গত প্রায় এক দশক ধরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার জিডিপির ২২/২৩ শতাংশে উঠানামা করছে। কাজেই মাত্র এক বছরের ব্যবধানে বিনিযোগ ৪/৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এটা আশা করা যায় না।
মাথাপিছু আয় গত অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশের মানুষের মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় ছিল ২ হাজার ৭৪৯ মার্কিন ডলার। যা গত অর্থবছরে ২ হাজার ৭৩৮ মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সংশয় রয়েছে। বিগত সরকার কৃতিত্ব প্রদর্শনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য প্রদর্শনের লক্ষ্যে মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় বেশি করে দেখাতো। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় ছিল ২ হাজার ২৪ মার্কিন ডলার। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তা ২ হাজার ৫৯১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। এটা কি বিশ^াসযোগ্য?
বিগত সরকারের আমলে দেশের ব্যাংকিং খাত সবচেয়ে ক্ষতিগস্ত হয়েছে। বিশেষ করে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কৃত্রিমভাবে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান মোতাবেক, দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ২ লাখ ৮৪ হাজার কোটি টাকার মতো। কিন্তু অবলোপনকৃত ঋণ হিসাবে পাওনা, পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ হিসাবের পাওনা এবং মামলাধীন প্রকল্পের নিকট পাওনা খেলাপি ঋণের পরিমাণ যোগ করা হলে প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬ লাখ কোটি টাকা অতিক্রম করে যাবে বলে অনেকেই মনে করছেন।
অর্থনীতিবিদগণ বলছেন, বর্তমান মুহূর্তে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে জনমনে স্বস্তি দেয়াই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কারণ তিন বছর ধরে চলা উচ্চ মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তাই যে কোনো মূল্যেই হোক উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি প্রবণতা রোধ করা যাবে না। উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমানো না গেলে সরকারের যে কোনো সাফল্য চরমভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।
চলতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অর্জনের প্রত্যাশা করা হয়েছিল তা পরিমার্জিত করে যৌক্তিকভাবে পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে।