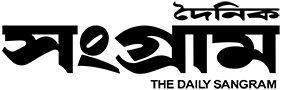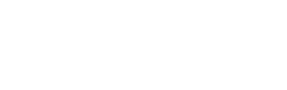রাজনীতি
নতুন দলের প্রধান হচ্ছেন নাহিদ
গত ই অগাস্ট শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর থেকেই শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে নতুন দল গঠনের গুঞ্জন শুরু হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেশজুড়ে কমিটি গঠন করতে শুরু করে এবং জাতীয় নাগরিক কমিটিও থানা পর্যায় পর্যন্ত সংগঠন বিস্তৃত করছে।

মানবজমিনের প্রথম পাতার শিরোনাম,
'নাহিদই হচ্ছেন নতুন দলের প্রধান'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের আলোচনা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। নিশ্চিত হওয়া গেছে, নতুন দলের প্রধান হবেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।
তিনি দায়িত্ব নেওয়ার আগেই সরকার থেকে পদত্যাগ করবেন, যা খুব দ্রুতই ঘটবে। তবে সরকারে থাকা অন্য দুই ছাত্র প্রতিনিধি এখনই পদত্যাগ করবেন না, তারা নির্বাচনের আগে তা করবেন।
গত ই অগাস্ট শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর থেকেই শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে নতুন দল গঠনের গুঞ্জন শুরু হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেশজুড়ে কমিটি গঠন করতে শুরু করে এবং জাতীয় নাগরিক কমিটিও থানা পর্যায় পর্যন্ত সংগঠন বিস্তৃত করছে।
মূলত এই ছাত্র আন্দোলন, নাগরিক কমিটি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মিলিয়ে নতুন দল তৈরি হবে। দলটি প্রথমে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।
বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব স্বাভাবিক ঘটনা হলেও বেশিরভাগ দল রাজনীতিতে বড় কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।
ছাত্রদের নেতৃত্বে আসা এই নতুন দল সত্যিই রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিবর্তন আনতে পারবে কি না, তা নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। এখন সবার দৃষ্টি নতুন এই দলের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকে।
সমকালের প্রধান শিরোনাম,
'অভিযানে গেলে নাকাল উভয় সংকটে পুলিশ'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, পুলিশ এখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। অপরাধী ধরতে গিয়ে তারা হামলার শিকার হচ্ছে, বাধার মুখে পড়ছে।
কোথাও তাদের ঘেরাও করে আসামি ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, আবার কোথাও থানায় ভাঙচুর চলছে এসব কারণে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারছে না।
কখনো তারা নীরব দর্শক হয়ে থাকছে, আবার কখনো দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছাচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষও বিভ্রান্তিতে পড়ছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। অনেক পুলিশ সদস্য শারীরিক ও মানসিক চাপে আছেন। তারা কঠোর ব্যবস্থা নিতে ভয় পান, কারণ এতে তারা প্রশাসনিক জবাবদিহির মুখে পড়তে পারেন।
কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত নিতে দোটানায় পড়েন।
সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোতে দেখা গেছে, চট্টগ্রাম, ঢাকা, লক্ষ্মীপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে। কখনো আসামি ধরতে গিয়ে, কখনো বিক্ষোভ বা আন্দোলন ঠেকাতে গিয়ে তারা বিপদে পড়েছে।
বিভিন্ন থানায় হামলা, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনা নিয়মিত ঘটছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পুলিশের মনোবল পুনরুদ্ধার ও আইনের কঠোর প্রয়োগ জরুরি। অপরাধীরা যদি মনে করে তারা শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারবে, তবে সমাজে বিশৃঙ্খলা আরও বাড়বে।
নিউ এইজের প্রধান শিরোনাম,
'1,308 arrested, mostly AL activists' অর্থাৎ, '১,৩০৮ জন গ্রেপ্তার, বেশিরভাগই আওয়ামী লীগ কর্মী'।
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, অপারেশন ডেভিল হান্ট নামে এক বিশেষ অভিযানে রোববার দেশজুড়ে ১,৩০৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী।
শনিবার রাত থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত পুলিশের নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনী এই অভিযান চালায়।
সরকার এই অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় গাজীপুরে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার পর, যেখানে ১৫ জন আহত হন। রোববার সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নজরদারির জন্য একটি কমান্ড সেন্টার চালু করে।
সরকারের উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানান, যারা দেশে অস্থিতিশীলতা তৈরি করছে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে।
গাজীপুরে ৮৩ জনসহ ঢাকা ও অন্যান্য শহরে বহু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন। গাজীপুরে অনেকে আত্মগোপন করেছেন।
সেখানে আওয়ামী লীগের বাড়িঘর ও অফিসে হামলা চালানো হয়। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গাজীপুর সদর থানায় ২৩৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
এছাড়া, দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও ছাত্রলীগের সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকার নিরাপত্তা বাহিনীকে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এই অভিযানে পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য বাহিনী একসঙ্গে কাজ করছে।
যুগান্তরের প্রধান শিরোনাম,
'আলোচনার টেবিলেই সমাধানের পথ'।
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে এবং তারা সমাধান খুঁজতে আলোচনার টেবিলে বসবে।
তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কোন সুপারিশ এখনই বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং কোনগুলো ভবিষ্যতে নির্বাচিত সরকার বাস্তবায়ন করবে।
বিশেষ করে সংবিধান পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নেতারা আরও চিন্তাভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিতে চান এবং এটি নির্বাচিত সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে চান।
শনিবার ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেছেন, এসব সুপারিশ চূড়ান্ত নয়, সরকার কোন সুপারিশ গ্রহণ করবে তা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হবে।
রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। চলতি মাসের মাঝামাঝি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এ বিষয়ে সংলাপ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
সংবিধান সংস্কার কমিশন নতুন কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে, যেমন সংসদের মেয়াদ চার বছর করা, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালু করা, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ দুইবারের বেশি না রাখা ইত্যাদি।
এছাড়া নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন 'না ভোট', গণভোট এবং অনলাইন ভোটিংয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো বলছে, অনেক সুপারিশ গ্রহণযোগ্য, তবে সংবিধান সংশোধনের মতো বড় সিদ্ধান্ত জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। আগামী নির্বাচনের পথে এই সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
নয়া দিগন্তের প্রধান শিরোনাম,
'আগে স্থানীয় নির্বাচন চায় ৬৫% মানুষ'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে যে, জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন অন্তর্বর্তী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ চার মাস নির্ধারণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী, ৬৫ শতাংশ মানুষ স্থানীয় নির্বাচনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে চায়, যেখানে ২৮ শতাংশ এর বিরোধিতা করেছে।
কমিশনের মতে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংস্কার এবং প্রশাসনিক পরিবর্তন আনতে পারবে।
তারা একটি স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্ধারণ করবে। এছাড়া, সংসদে পাসের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা তৈরি করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।
কমিশন বলেছে, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন করা দরকার এবং তা নির্দলীয় ভিত্তিতে হওয়া উচিত। মেয়র, চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে।
এছাড়া, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বাজেটের ৩০ শতাংশ বরাদ্দ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
জরিপে অংশ নেওয়া অধিকাংশ মানুষ মনে করেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন হলে সেগুলো আরও গ্রহণযোগ্য হবে এবং ভালো প্রার্থীরা নির্বাচিত হতে পারবেন।
প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম,
'বিসিএস পরীক্ষা–নিয়োগ দেড় বছরে শেষ করার সুপারিশ'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, যদি দেড় বছরের মধ্যে বিসিএস পরীক্ষার নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব হয়, তাহলে তা চাকরিপ্রার্থীদের জন্য একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হবে।
৪১তম ও ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চার বছরের বেশি সময় লেগেছে। দীর্ঘসূত্রতা কমাতে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন দেড় বছরের মধ্যে পরীক্ষা ও নিয়োগ শেষ করার সুপারিশ করেছে।
এক বছরের মধ্যে প্রিলিমিনারি, লিখিত, মৌখিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা নিয়ে ছয় মাসের মধ্যে চূড়ান্ত ফল ও নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে।
৪১তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি ২০১৯ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত হয়, কিন্তু চূড়ান্ত নিয়োগ সম্পন্ন হতে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত লেগেছে।
কমিশনের প্রতিবেদনে ভারতের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার তুলনা টেনে দেখানো হয়েছে, সেখানে এক বছরের মধ্যেই নিয়োগ শেষ হয়।
কমিশন বলেছে, পিএসসি সময় অপচয় করছে, ফলে লাখো শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। নির্দিষ্ট পঞ্জিকা না থাকায় পরীক্ষা ও ফল প্রকাশে বিলম্ব হয়।
কমিশন প্রতি বছর জানুয়ারিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দেড় বছরের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করার সময়সূচি নির্ধারণের সুপারিশ করেছে।
সিলেবাস পরিবর্তন, পুলিশ ভেরিফিকেশন পদ্ধতি সহজ করা ও তিনটি পিএসসি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। পিএসসি চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, এসব পরিবর্তন হলে ১৪ মাসেই বিসিএস পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব হবে।
বণিক বার্তার প্রধান শিরোনাম,
'ছয় মাস ধরে শিক্ষা খাতের বড় সিদ্ধান্তগুলো মবকে ঘিরে'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও শিক্ষা খাতে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার হয়নি।
ছয়টি কমিশন গঠন করা হলেও শিক্ষা খাত উপেক্ষিত থেকেছে। অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আন্দোলনের চাপে, যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।
এইচএসসি ও সমমানের স্থগিত পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে সরকার পরীক্ষা বাতিল করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
শিক্ষা খাত নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব স্পষ্ট। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলছেন, চাপের মুখে নেওয়া সিদ্ধান্ত দেশের জন্য ক্ষতিকর।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সাত কলেজের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আন্দোলনের ফলে সরকার বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। একইভাবে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পর ডাকসু ও জাকসু নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত আসে।
পাঠ্যক্রম নিয়েও বিতর্ক হয়েছে। নতুন কারিকুলাম বাতিল করে পুরনো পাঠ্যক্রমে ফিরে যাওয়া হয়। একটি সংগঠনের দাবিতে 'আদিবাসী' শব্দটি পাঠ্যবই থেকে বাদ দেওয়া হয়।
শিক্ষকরা আন্দোলনের মাধ্যমে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত আদায় করেন। তবে শিক্ষা
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্দোলনের মুখে নেওয়া সিদ্ধান্তের কারণে শিক্ষা খাত আরও দুর্বল হচ্ছে। সরকারের উচিত পরিকল্পিত সংস্কার নিশ্চিত করা।
কালের কণ্ঠের প্রধান শিরোনাম,
'রোজা ঘিরে পর্যাপ্ত পণ্য আমদানি'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, রমজান মাস শুরু হতে আর কিছুদিন বাকি। এ সময় বাজারে ছোলা, খেজুর, ডাল, পেঁয়াজ, চিনি ও ভোজ্যতেলের চাহিদা বেড়ে যায়।
ব্যবসায়ীরা আগেই প্রস্তুতি নিয়েছেন, ফলে জানুয়ারিতে প্রচুর পরিমাণে এসব পণ্য আমদানি হয়েছে। এতে রোজার সময় বাজারে কোনো সংকট হওয়ার সম্ভাবনা কম।
তবে ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও আমদানি বেড়েছে, তারপরও বোতলজাত সয়াবিন তেল কিছু দোকানে কম পাওয়া যাচ্ছে।
কোথাও কোথাও বাড়তি দাম চাওয়া হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ডলার সংকট ও পাম তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে সয়াবিন তেলের চাহিদা বেড়েছে, যা সংকট তৈরি করছে।
বাকি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ভালো। রাজধানীর বাজারগুলোতে চিনি, ছোলা, ডাল, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম তুলনামূলক স্থিতিশীল রয়েছে। সরকার শুল্ক কমিয়ে আমদানি সহজ করেছে, ফলে পণ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা কম।
ব্যবসায়ীরা আশ্বস্ত করেছেন, রোজায় ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়বে না। তবে কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, যেন কৃত্রিম সংকট তৈরি না করা হয়।
সব মিলিয়ে রমজানে বাজার পরিস্থিতি ভালো থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক করতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।